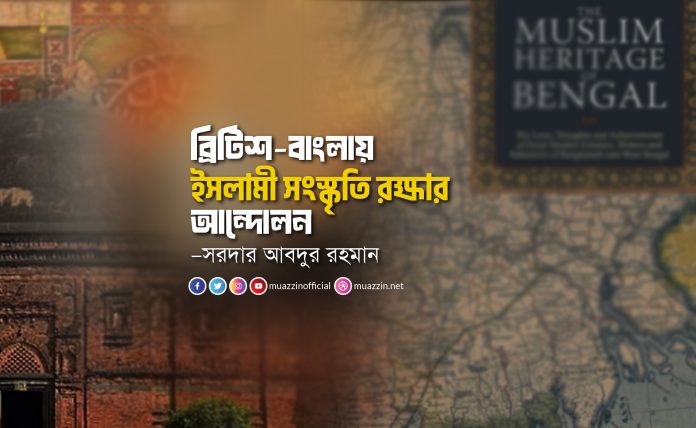সরদার আবদুর রহমান |
সংস্কৃতি মূলত বিশ্বাসেরই প্রতিরূপ। প্রতিটি জাতি তার সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং তা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। বিদ্যজনেরা বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর সবকিছুই সংস্কৃতির অংশ। তবে ইসলামের বেলায় পার্থক্য হলো, সেই সংস্কৃতি যদি মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা হবে অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
একজন পণ্ডিতের মতে, সংস্কৃতি শব্দের অর্থ সংশোধন, শুদ্ধিকরণ, বিশোধন, উৎকর্ষ সাধন, উদ্ধারকরণ, উন্নতি সাধন ইত্যাদি। সংস্কৃতির আরবি প্রতিশব্দ ‘সাকাফা’, যার অর্থ প্রশিক্ষণ পাওয়া, সফল হওয়া। পরিশীলিত, প্রশিক্ষিত, মার্জিত, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও রুচিশীল ব্যক্তিকে বলা হয় মুসাক্কাফ বা সংস্কৃতিবান। ইংরেজি ভাষায় সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হিসেবে কালচার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কালচার অর্থ কর্ষণ করা। কৃষক জমিতে চাষ দিয়ে বা কর্ষণ করে যেমনি ফসল উৎপাদনের উপযোগী করেন, তেমনি মানুষ উত্তম আচার-আচরণের অনুশীলনের মাধ্যমে পরিশীলিত ও সংস্কৃতিবান হয়। এ ছাড়া শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে আরবি ও উর্দু ভাষায় তাহজিব ও তমদ্দুন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এককথায় উন্নত, মার্জিত, পরিশীলিত জীবনাচারকে সংস্কৃতি বলা হয়। ইসলামী শরিয়ত অনুমোদিত তথা কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত জীবনাচারকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। কোরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে যে আচার-আচরণ প্রতিফলিত হয় তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি।
যা হোক, এই প্রবন্ধে ‘সংস্কৃতি’ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। এখানে মুসলিম জাতির যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য- যাকে তারা জীবনের অপরিহার্য অংশ মনে করে- তা বারে বারে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এই ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি কীভাবে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর অবস্থায় নিপতিত হয় এবং তা রক্ষা করতে কোন ধরণের আন্দোলন গড়ে ওঠে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের মুসলিম অধ্যূষিত অঞ্চলসমূহে মূলত পলাশীযুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে। ব্রিটিশ শক্তি মুসলমানের ক্ষমতা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি খর্ব করার জন্য অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা গ্রহণ করে। এজন্য তারা পাশে নেয় এদেশীয় হিন্দু জমিদার ও ধনিক শ্রেণিকে। এর পরিণতি হয় খুবই ভয়াবহ। যে কোন জাতির শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নয়নের পেছনে থাকে আর্থিক আনুকূল্য ও সাহায্য-সহযোগিতা। এর মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক বিচ্যূতির পথও সুগম হয়। বলাবাহুল্য, ‘পলাশীর ময়দানে বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্ত হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ‘রাজনৈতিক অর্থনীতি’ ভেঙে পড়ে, গোটা দেশ দারিদ্র ও দুঃখ-দুর্দশা কবলিত হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে ধ্বংসের ভয়াবহতা। কোম্পানি-শাসনের প্রথম দিকেই বাংলার মুসলমানগণ বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।’ (আব্বাস আলী খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস)। ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এদেশে তাদের ভিত্তি শক্ত করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর ফলে অন্যদের বেলায় যাই ঘটুক, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বড় আঘাত হিসেবে আপতিত হয়। ইংরেজরা এক্ষেত্রে নানা কৌশল গ্রহণ করে। একটি রিপোর্টে তার নমুনা পাওয়া যায়। মিশনারীদের বক্তব্য ছিল, “ব্যবসা-বাণিজ্য এক নতুন চিন্তাধারার উন্মোচন করে দিয়েছে। যদি আমরা দক্ষতার সাথে অবৈতনিক শিক্ষাদান করতে পারি তাহলে শত শত লোক ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করার জন্য ভীড় জমাবে। আশা করি তা আমরা এক সময়ে করতে সক্ষম হবো এবং এর দ্বারা যীশুখ্রিষ্টের বাণী প্রচারের এক আনন্দদায়ক পথ উন্মুক্ত হবে।” (মিশনারী রিপোর্ট-এর উদ্বৃতি : এম ফজলুর রহমান, বেঙ্গলি মুসলিম এন্ড ইংলিশ এডুকেশন)। ‘উইলিয়াম কেরীর সভাপতিত্বে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর (হুগলি) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান দান করা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশের লোককে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা।’(পূর্বোক্ত)
সে সময় যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সিলেবাস পড়ানোর ব্যবস্থা করা হতো সেগুলোর লক্ষ্যই ছিল হিন্দুদের সুবিধা প্রদান এবং মুসলমানদের বঞ্চিত রাখা। “মাতৃভাষার স্কুলগুলোতে সংস্কৃতি শব্দবহুল বাংলা পড়ানো হতো- এসব স্কুলের দ্বার মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ ছিল। আবার বিহারে হিন্দি ভাষা দেবনাগরী বর্ণমালা শিখানো হতো এবং সেটাও ছিল মুসলমানদের কাছে একেবারে অপরিচিত।’ (রিপোর্ট অব বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কমিটি, এডুকেশন কমিশন)।
উপরন্তু এসব স্কুলে বাংলা ভাষায় যে সব পাঠ্যপুস্তক ছিল তা সবই হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত। বাংলা ভাষায় সাধারণত নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ানো হতো : গুরুদক্ষিণা, অমর সিংহ, চাণক্য, স্বরস্বতী বন্দনা, মানভঞ্জন, কলংকভঞ্জন প্রভৃতি। হিন্দু বই যথা- দানশীলা, দধিলীলা প্রভৃতি- যা ছিল কৃষ্ণের বাল্যকালের প্রেমলীলা সম্পর্কে লিখিত। বিহারে এতদ্ব্যতীত পড়ানো হতো সুদাম চরিত, রামযমুনা প্রভৃতি। (এ. আর. মল্লিক : ব্রিটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিম ইন বেঙ্গল)।
উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ প্রমাণ করে, মুসলমানদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখার জন্য খ্রিষ্টান মিশনারী, ইংরেজ শাসক ও এ দেশীয় দালালেরা ছিল একাট্টা। হিন্দু শিক্ষকদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-পদ্ধতি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। আর এ ধরনের বাংলা ভাষা মুসলমানদের কাছে ছিল অপরিচিত। যদিও বাংলার এক বিরাট অংশের মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতিকে টার্গেট করে। বলতে গেলে এরই জের ধরে পরবর্তীকালে উর্দুকেও টার্গেট করে ফেলা হয় বিদেশি ভাষা বলে। কারণ, কুরআন-হাদিসের অনুবাদ-সাহিত্য মূলত উর্দু নির্ভর ছিল। উর্দুকে নির্বাসিত করতে পারলে মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন ও চিন্তার বিকাশকে পঙ্গু করে ফেলা সম্ভব হবে। এই ভাবনা থেকেই ষাট-সত্তর দশক জুড়ে উর্দূ হঠানোর জন্য সংগ্রাম শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজ্জ্বাধারীরা।
এই প্রক্রিয়ার নমুনা সেই ব্রিটিশকালে দেখা যায়। আরবি-পারসিতে অশুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য সেকালে কয়েকটি অভিধান রচিত ও প্রকাশিত হয়। সাহেবরা সুবিধা পেলেই আরবি ও পারসির বিরোধিতা করে বাংলা-সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিতেন, ফলে দশ-পনের বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণই পরিবর্তিত হয়ে যায়।
ইংরেজরা উপলব্ধি করেছিল, মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে দাবিয়ে রাখতে হলে তাঁদের ভাষারও গোড়া কেটে দিতে হবে। ইংরেজ তথা মিশনারি-পূর্ব বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে মুসলমানদের যে এক নতুন বাংলা ভাষা গড়ে উঠে, যার মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিল আরবি-ফারসি, তাকে বলা যেতে পরে মুসলমানী বাংলা। স্বভাবতই তা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না হিন্দুদের কাছে। ১৮৩৭ সালের পর হিন্দুবাংলা (আরবি-ফার্সি শব্দ বর্জিত সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা) প্রাদেশিক মাতৃভাষা হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর মুসলমানী বাংলার অগ্রগতির পথ রূদ্ধ হয়। অফিস-আদালত থেকে এতদিনের প্রচলিত ফার্সিভাষা তার আপন মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং নতুন বোধনকৃত বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকে। নতুন বাংলা ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর এ ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয় আশা-আকাক্সক্ষার বাহন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। (আব্বাস আলী খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৮৫)।
পলাশী-পরাজয়ের প্রভাব এতো দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মুসলমানদের ভেতরে কোন সংস্কার কাজ পর্যন্ত সহ্য করা হতো না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মীর নিসার আলী তিতুমীরের এমনি সংস্কার আন্দোলনে সমকালে হিন্দু জমিদার ইসলামের সংস্কৃতির উপর সরাসরি আঘাত হেনে বসে। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ফরমান জারি করে: (১) যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাটবে তাদের দাড়ির জন্য আড়াই টাকা এবং গোঁফের জন্য পাঁচসিকা করে খাজনা দিতে হবে। (২) মসজিদ তৈরি করলে কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশ’ টাকা এবং প্রতি পাকা মসজিদের জন্য এক হাজার টাকা করে জমিদারকে কর দিতে হবে। (৩) আরবি নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদারকে জমা দিতে হবে। (৪) গরু হত্যা করলে তার ডান হাত কেটে নেওয়া হবে- যাতে আর কোনোদিন গো-হত্যা করতে না পারে। মুসলমানদের উপর এ ধরনের অত্যাচার চালানোর জন্য অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল তারাগুনিয়ার জমিদার রামনারায়ণ, কুরগাছির জমিদারের নায়েব গৌরপ্রসাদ চৌধুরী, পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় প্রমুখ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পলাশীপূর্বকালে এ ধরনের অত্যাচার-নিপীড়নের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না।
কুসংস্কার ও অনাচার
এদিকে, বাংলার কোনো কোনো হিন্দু বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক-সাধকদের নানা কুসংস্কার ও অনাচারমূলক কার্যকলাপের প্রভাবে-প্রতাপে মুসলমানরাও দিগভ্রান্ত হয়। এতে তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত হয়। বিশেষ করে শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মমত প্রবর্তনের ফলে হিন্দুজাতির চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা, মুণ্ডিত কেশ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের জঘন্য যৌন-অনাচারের স্রােত প্রবহিত হয়। যা শুধু হিন্দু সমাজের বৃহৎ অংশকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, অশিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদেরকেও এদিকে আকৃষ্ট করে। তারাও ধর্মের নামে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার গর্তে পতিত হয়।
অন্যদিকে, মুসলমানদের নামকরণের উপরেও তারা হস্তক্ষেপ করলো। “বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা’র নামে এই বিপদগামীতা প্রকাশ পায়। হিন্দু ঠাকুর মশায়রা বলা শুরু করলো, তোমরা বাপু মুসলমান হলেও বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তেমনি বাংলা নামের প্রয়োজন। অতএব ঠাকুর মশায়ের ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমানদের নাম রাখা হতে লাগলো, গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন, নবাই, কুশাই, পদ্মা, চিনি, চাঁপা, বাদল, পটল, মুক্তা প্রভৃতি।” (আব্বাস আলী খান : বাংলা মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২১৭)। বাংলার হিন্দু জাতি ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এবং আপন মাতৃভূমির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদেরকে শুধু রাজ্যচূত্যই করেনি, জীবিকা অর্জনের সকল পথ রুদ্ধ করেছে এবং একজন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ঈমানটুকুও নষ্ট করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। মুসলমানদেরকে নামে মাত্র মুসলমান রেখে ঈমান, ইসলামী জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে নিক্ষেপ করে নিম্ন শ্রেণির হিন্দু অপেক্ষাও এক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তাদেরকে দাসানুদাসে পরিণত করতে চেয়েছিল। (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩) এখানেই শেষ নয়, ‘মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতা ও বিধর্মী ভাবধারার অনুপ্রবেশ যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা পরিপূর্ণ করে দেয় এক শ্রেণির ভণ্ড পীর-ফকীরের দল। এমনকি ধর্মের নামে তারা বৈষ্ণব ও বামাচারী তান্ত্রিকদের অনুকরণে যৌন অনাচারের আমদানিও করে।’
উপরে বর্ণিত জঘন্য ও নোংরা পরিবেশের প্রভাবে বাংলার তৎকালীন মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতন এবং সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিশৃঙ্খলার এক অতি শোচনীয় স্তরে নেমে আসে। এ অধঃপতনের চিত্র পাঠক সমাজে পরিস্ফুট করে তুলে ধরতে হলে এখানে মুসলমান নামধারী মারফতি বা নেড়া পীর-ফকীরদের সাধন পদ্ধতির উল্লেখ প্রয়োজন। এ ভণ্ড ফকীরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যথা আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি। এগুলো হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা যায়। (আব্বাস আলী খান : বাংলা মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২১৭)। বৈষ্ণববাদ বাংলার মুসলমানদের যে ক্ষতি করে তার একটি চিত্র দিয়েছেন মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর ‘মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থে।
ইতিহাসের এসব উদ্ধৃতি ও ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হয় যে, পলাশী যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, মূল্যবোধ, চেতনা, দৈনন্দিন আচার ও সংস্কৃতির উপর এক বিধ্বংসী আঘাতের মতোই। এটা একদিকে মুসলমানদেরকে হতাশার গভীরে নিমজ্জিত করে, আবার হিন্দু-খ্রিষ্টান উজ্জীবন ঘটায়। অর্ধসহ¯্র বছরের গড়ে ওঠা সংস্কৃতি এক রাহুগ্রাসে তলিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানিসহ ইতিহাসের নায়কদের কর্মপ্রচেষ্টা মুসলমানদের পুনঃজাগরণের পথে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়। সৈয়দ আহমদ বেরলবীর বালাকোট আন্দোলন, শরীয়তুল্লাহ’র ফারায়েজি আন্দোলন, শহীদ তিতুমীরের সংগ্রাম প্রভৃতি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। যদিও ইংরেজ ও সহযোগী শক্তি এসব আন্দোলন নস্যাতের নানা প্রচেষ্টা নিয়েছে। তথাপি পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য তা পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে- একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি পলাশী যুদ্ধের দ্বারা ঘটে যায় তার পূরণ আজো হয়নি সেটাও অবধারিত সত্য।
ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলনের নায়ক
এখানে যদি নমুনা হিসেবে শুধু তিতুমীরের আন্দোলনের পটভূমি উল্লেখ করা হয় তাহলে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে। বাংলার বীর সাইয়েদ মীর নেসার আলী তিতুমীরকে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে পরিচয় করানো হলেও তিনি একাধারে ইসলামী সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলনেরও নায়ক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মুসলমানদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পূঁজার পাঁঠা জোগাতে হতো, কেউ দাঁড়ি রাখলে সেজন্য চাঁদা দিতে হতো, মসজিদ নির্মাণ করলে কর দিতে হতো, এমনকি কেউ গরু জবাই করলে তার ডান হাত কেটে দেয়ার ঘটনাও কম ছিল না। এই পটভূমিতে দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের পক্ষে প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে তোলেন তিতুমীর। তাঁর পরিচালিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এক পর্যায়ে ইংরেজ বিরোধী স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। তিনি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে তিনি জনগণকে সচেতন করতে থাকেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রচারকাজে অভাবিত জাগরণ দেখা দেয়। ধর্মীয় অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া- এই দু’টি ছিল তাঁর মৌলিক কর্মসূচি। তাঁর আহবান ছিল বিরাণ হয়ে যাওয়া মসজিদ সংস্কার করে নামাজের ব্যবস্থা করা, পূজার চাঁদা দান কিংবা তাতে অংশ নেওয়া থেকে মুসলমানদের বিরত রাখা, শিরক-বিদাত হতে দূরে থাকা, মুসলমানদের মুসলিম নাম রাখা, মুসলমানদের ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি বা পাজামা পরা, পীরপূজা ও কবরপূজা না করা ইত্যাদি। তিতুমীরের ধর্মীয় দাওয়াতের মূলকথা ছিল, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুল (স.)-এর নির্দেশ পরিপালন সম্পর্কিত। এটি ছিল মূলত ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন পূনর্গঠনের এক বৈপ্লবিক কর্মসূচি। বলা বাহুল্য, তা ছিল একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও।
এই অভাবনীয় আহবানের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নির্যাতিত দরিদ্র কৃষকদের সমন্বয়ে একটি দল। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম বিরোধিতায় নামেন জমিদাররা। বিশেষ করে পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রী দেবনাথ রায়, ধান্যকুড়িয়ার জমিদার শ্রী রায়বল্লভ, তারাগুনিয়ার শ্রী রাম নারায়ন নাগ, নাগরপুরের জমিদার গৌর প্রসাদ চৌধুরী, সরফরাজপুরের জমিদার শ্রী কে.পি মুখার্জী ও কোলকাতার গোমস্তা লালু বাবু প্রমুখ তিতুমীর ও তার সঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ইংরেজ নীলকররাও ছিল জমিদারদের পক্ষে। পূঁড়ার জমিদার তিতুমীরের সঙ্গী-সাথীদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। তিতুমীর ঐ জমিদারকে পত্র মারফত জানান যে, তিনি (তিতুমীর) কোনো অন্যায় করছেন না, ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এই কাজে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। এটা পরধর্মে হস্তক্ষেপের সামিল হবে। তিতুমীরের এই পত্র নিয়ে জমিদারের কাছে গিয়েছিলেন আমিনুল্লাহ নামক একজন দূত। জমিদার তিতুমীরের পত্রকে কোনো তোয়াক্কা না করে তাঁর দূতকে নির্মমভাবে হত্যা করে। জমিদারের লোকেরা মুসলিম-প্রধান গ্রাম বশিরহাটের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় ও গ্রামটি লুট করে। সরফরাজপুরের মসজিদে তিতুমীর ও তার কয়েকজন অনুসারীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত তিতুমীর বেঁচে যান।
অনেকেই বলার চেষ্টা করেন, তিতুমীর সাধারণ একজন ‘লাঠিয়াল’ ছিলেন। আসলে তা নয়, তিতুমীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বাংলার নিরীহ মুসলমানদের এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে বারবার আক্রমণ করে শেষে জীবন রক্ষার জন্য হাতে লাঠি নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। দরিদ্র মুসলিম ও সাধারণ কৃষকদের পক্ষে কথা বলে তিতুমীর টিকে থাকতে পারেননি সত্য। তাই বলে তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ অব্যাহত ছিল। ঘটনার ২৫ বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী জনতার বিদ্রোহকেও ইংরেজ সরকার নির্মমভাবে দমন করেছিল। সেই ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। অত্যাচারী জমিদাররাও আর নেই। আছে শুধু তিতুমীর ও তার বীরত্বগাঁথা আর সংগ্রামের ইতিহাস। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তিতুমীরের কথা স্মরণ করে।
আরো সব বীরেরা
বিশিষ্ট লেখক ও অভিনেতা আরিফুল হক এই ইতিহাসকে আরো বিস্তৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর এক প্রবন্ধে তিনি আমাদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির লড়াইয়ের সৈনিক হিসেবে অনেকগুলো নাম যুক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, টিপু সুলতান, সিরাজউদ্দৌলা, মীরকাশিম, সৈয়দ নিসার আলি তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মজনু শাহ, দুদু মিয়া, নূর আহমদ, মিজানপুরী, কাজী মিয়াজান, হাবিলদার রজব আলি, পাগলা টিপু, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, শাহ সৈয়দ আব্দুল আজিজ, হাজী এমদাদ উল্লাহ প্রমুখ। আর লড়াইয়ের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করেছেন পলাশীর যুদ্ধ, বালাকোটের যুদ্ধ, বকসারের যুদ্ধ, সিপাহী বিপ্লব, ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নারকেল বাড়িয়ার প্রতিরোধ, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র ও সংসদীয় সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ, সাতচল্লিশ’র আন্দোলন প্রভৃতিকে। তিনি বর্তমান প্রজন্মের প্রতি ইঙ্গিত করে এও উল্লেখ করেছেন, বাঙালি মুসলমানদের আত্মবিকাশকে স্তব্ধ করার জন্য ‘বঙ্গ বিভাগ’ রদকল্পে ব্রিটিশদের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কংগ্রেসী নেতা সূর্যসেনকে ওরা আজাদীর হিরো হিসেবে জেনে এসেছে, কিন্তু জানে না সূর্যসেনের চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের দু’বছর আগে ১৯২৮ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজী বজলুর রহমান চট্রগ্রামের অত্যাচারী জেলা শাসক ডেভিডকে তার বাড়িতে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে নিহত করে ফাঁসীতে গিয়েছিলেন- সেই আত্মত্যাগের ইতিহাস। ওরা ক্ষুদিরামের গল্প জানে- কিন্তু জানে না, তরিকায়ে মহম্মদীয়া আন্দোলনের সেই দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ শের আলির কথা, যিনি দু’শো বছরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে একমাত্র বড়লাট লর্ড মেয়োকে লৌহশলাকায় এফোড় ওফোড় করে নিজে শহীদ হয়েছিলেন। ওরা অনেক রঙীন অসত্য ফ্যানটাসীর ইতিহাস জানে, শুধু জানে না নিজেদের সত্য সমুজ্জ্বল আড়াই হাজার বছরের আলোকিত ইতিহাস। ওরা জানে না আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বহমান এক মহান ধারাবাহিকতারই ইতিহাস। ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে আগত সুফী সুলতান বায়েজিদ বোস্তামী, সৈয়দ সুলতান মাহীসওয়ার, শাহ মুহম্মদ সুলতান রুমী, বাবা আদম শহীদ, শাহা নিয়ামতুল্লাহ বুৎশিকান, হজরত শাহজালাল (রহ) কিংবা বখতিয়ার খিলজি থেকে ইলিয়াস শাহী আমল পর্যন্ত আগত মুসলমান সুফী দরবেশ সাধক, নৃপতিগণ, অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে এদেশের অত্যাচারিত পদদলিত গণমানুষকে মুক্ত করে সাম্য সৌভ্রাতেৃত্বে আলোকিত পথে সমবেত করার মধ্য দিয়েই সূচনা করেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আজকের তরুণ সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস জানে না।
এতো গেল ব্রিটিশকালের কথা। আর আজ? এক অন্য রূপ-রঙ-সজ্জা নিয়ে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের নিজস্বতাকে গ্রাস করে চলেছে। বেতার-ইথারবাহিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নানান মাধ্যমে পরিবেশিত নাটক, সিনেমা, নৃত্য, সংগীত, মডেলিং, ফ্যাশন, অবৈধ প্রণয় কাহিনী ও দৃশ্যের চিত্রায়নসহ অসংখ্য উপকরণ হাতের নাগালে। বিশেষত, ভারতীয় পৌত্তলিক সংস্কৃতির বিপননের পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রচারবাহী বিভিন্ন ভিউজ্যুয়াল আইটেম আমাদেরকে নিত্য আচ্ছন্ন করে রাখছে। এর সঙ্গে যুক্ত ইন্টারনেট ও মোবাইল মাধ্যমে ধেয়ে আসা প্লাবন আমাদের যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বসেছে। এখানে এসব মাধ্যমের কোনো দোষ নেই বটে, কিন্তু সেগুলোর একতরফা ও একচেটিয়া ব্যবহার সেই প্লাবনকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের চিন্তাবিদদের কার্যকর মোকাবেলার কৌশল নিয়ে অগ্রসর হবার সময় যেন দ্রুতই ফুরিয়ে যাচ্ছে।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও কলামিস্ট